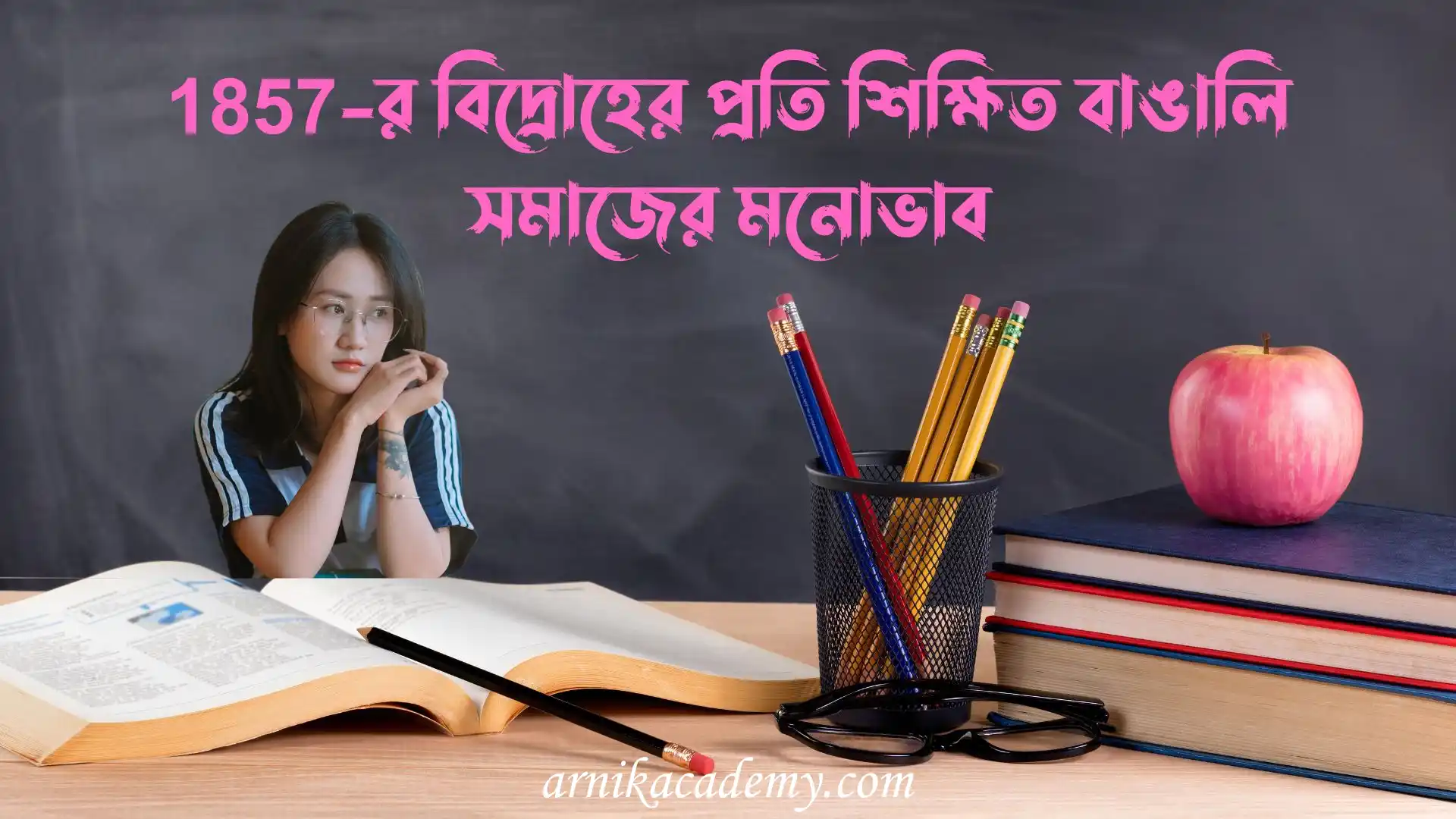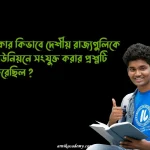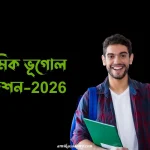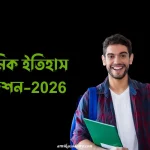১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের শিক্ষিত বাঙালি সমাজের মনোভাব কেমন ছিল তা আলোচনা করা হলো। যা মাধ্যমিক ছাত্র-ছাত্রীদের খুবই সাহায্য করবে।
১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের প্রতি শিক্ষিত বাঙালি সমাজের মনোভাবঃ
ভূমিকাঃ
উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতে আধুনিক শিক্ষার বিস্তার ঘটে। এই পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করে একদল শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান ঘটে। তারা ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের প্রতি দ্বিধান্বিত ছিল। তাদের মনোভাব গঠনে রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্য, এবং বিদ্রোহের নেতৃত্বের প্রকৃতি ভূমিকা রেখেছিল।
ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্যঃ
শিক্ষিত বাঙালি সমাজের একটা বড় অংশ বিশেষত কলকাতার ধনী শ্রেণি ও জমিদাররা, ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিল। তারা মনে করতেন ব্রিটিশ শাসন ভারতের পক্ষে কল্যানকর এবং সুশৃংখল। এজন্য তারা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের তীব্র বিরোধিতা করেছিল। এ প্রসঙ্গে বলা যায়-ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, শম্ভু চন্দ্র মুখার্জী, অক্ষয় কুমার দত্ত, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কিশোরী চাঁদ মিত্র। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট বাঙালিও এরও মনোভাব পোষণ করতো।
সিপাহী বিদ্রোহের বিরোধিতাঃ
বিদ্রোহের মাধ্যমে ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদের পর ভারতীয়রা এদেশে জাতীয় রাষ্ট্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে কিনা এ নিয়ে শিক্ষিত সমাজের আশঙ্কা ছিল। তাই ভারতের সর্বস্তরের মানুষ এই বিদ্রোহকে সমর্থন করলেও শিক্ষিত বাঙালি সমাজের একটা বড় অংশ এই বিদ্রোহকে সমর্থন করেনি
সামন্ততান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিঃ
১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ যখন ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন শিক্ষিত বাঙালি সমাজের সমর্থনের অভাবে বাংলায় তা খুব একটা শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারেনি। কারণ শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটা অংশ মনে করেছিল যে, বিদ্রোহীরা সফল হলে ভারতে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।
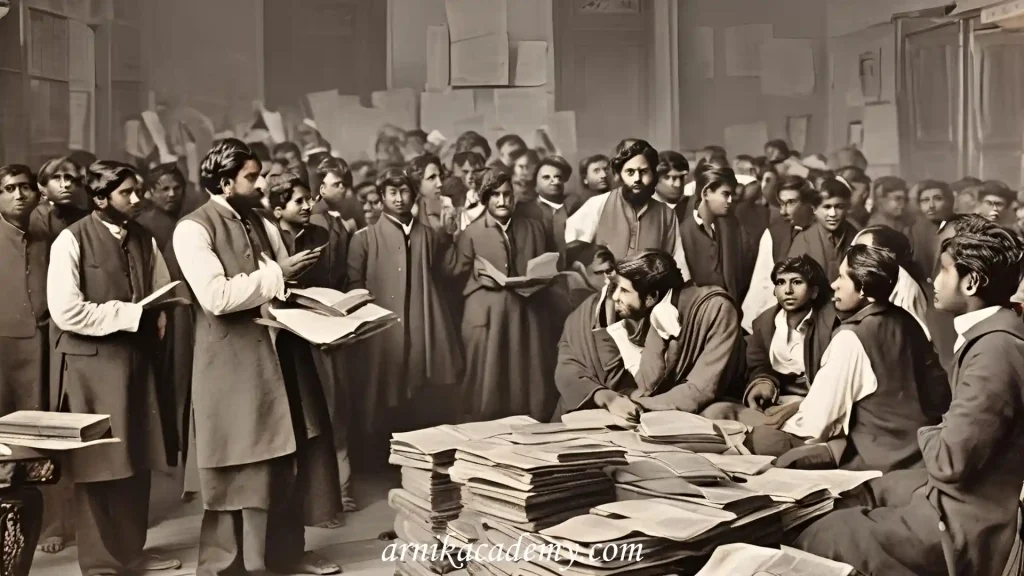
বিভিন্ন বাঙ্গালীদের অভিমতঃ
মহাবিদ্রোহ সম্পর্কে বিভিন্ন খ্যাতনামা বাঙালি পন্ডিত বিভিন্ন মত দিয়েছেন। যেমনঃ হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তার হিন্দু প্যাট্রিয়টে বিদ্রোহীদের বর্বর, নরহত্যাকারী, দুষ্টু বলে অভিহিত করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এই বিদ্রোহী জনগণের সমর্থন ছিল না। অন্যদিকে রাজনারায়ণ বসু এই বিদ্রোহকে নৈরাজ্যবাদী, অন্যায়কারী দানব বলে অভিহিত করেছিলেন। শিক্ষিত বাঙালির এরূপ মন্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, তারা এই বিদ্রোহকে সমর্থন করতেন না।
গণমানুষের প্রতি সহানুভূতিঃ
যদিও শিক্ষিত সমাজের একটি অংশ বিদ্রোহে সরাসরি সমর্থন জানায়নি, আবার অনেকে সাধারণ মানুষের দুর্দশা উপলব্ধি করেছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় ব্রিটিশ শাসনের প্রতি সমালোচনার প্রকাশ পায়।
উপসংহারঃ
১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের প্রতি শিক্ষিত বাঙালি সমাজের মনোভাব জটিল ও মিশ্র ছিল। বিদ্রোহ দমনে সহিংসতা এবং ব্রিটিশ শাসনের কুফল তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রভাব ফেলেছিল। যার জন্য পরবর্তী কালে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি তাদের সমর্থন কমে যায় এবং জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে।
1855 খ্রিস্টাব্দে সাঁওতাল বিদ্রোহ কেন হয়েছিল? প্রশ্নের উত্তরটি দেখতে Click করুন এখানে।
তথ্যসূত্রঃ
এই ব্লগের কাজ করতে Wikipedia এর সাহায্য নেয়া হয়েছে।
কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তরঃ
প্রশ্ন: ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ কী?
উত্তর: ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম বৃহৎ সশস্ত্র আন্দোলন। এটি সিপাহী বিদ্রোহ নামে পরিচিত এবং বিভিন্ন অঞ্চলে এটি ভিন্ন প্রকৃতি ধারণ করেছিল।
প্রশ্ন: শিক্ষিত বাঙালি সমাজের একাংশ ব্রিটিশ শাসনকে কেন সমর্থন করেছিল?
উত্তর: শিক্ষিত বাঙালি সমাজের একাংশ ব্রিটিশ শাসনকে সুশৃঙ্খল ও কল্যাণকর মনে করেছিল। তারা মনে করত, ব্রিটিশ শাসন ভারতে স্থিতিশীলতা ও আধুনিকতার পথ সুগম করবে।
প্রশ্ন: শিক্ষিত বাঙালি সমাজ সিপাহী বিদ্রোহকে কীভাবে দেখেছিল?
উত্তর: শিক্ষিত বাঙালি সমাজ সিপাহী বিদ্রোহকে বর্বর ও বিশৃঙ্খল বলে মনে করেছিল এবং এর মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নিয়ে সন্দিহান ছিল।
প্রশ্ন: বিদ্রোহের প্রতি হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল?
উত্তর: হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তার হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকায় বিদ্রোহীদের বর্বর ও নরহত্যাকারী বলে অভিহিত করেছিলেন।
প্রশ্ন: রাজনারায়ণ বসু বিদ্রোহ সম্পর্কে কী বলেছেন?
উত্তর: রাজনারায়ণ বসু ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহকে নৈরাজ্যবাদী এবং অন্যায়কারী দানব বলে অভিহিত করেছিলেন।
প্রশ্ন: শিক্ষিত বাঙালি সমাজ বিদ্রোহকে সামন্ততান্ত্রিক অভ্যুত্থান কেন মনে করত?
উত্তর: শিক্ষিত বাঙালিরা মনে করত, বিদ্রোহীরা সফল হলে ভারতে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।
প্রশ্ন: বিদ্রোহের প্রতি গণমানুষের প্রতি শিক্ষিত বাঙালির সহানুভূতির উদাহরণ কী?
উত্তর: মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাদের লেখায় ব্রিটিশ শাসনের প্রতি সমালোচনা করে সাধারণ মানুষের দুর্দশার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন।
প্রশ্ন: ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে বাংলায় কেন বড় প্রভাব পড়েনি?
উত্তর: শিক্ষিত বাঙালি সমাজের সমর্থন না পাওয়া এবং বাংলার বিশেষ পরিস্থিতি বিদ্রোহকে এখানে তেমন শক্তিশালী হতে দেয়নি।
প্রশ্ন: বিদ্রোহের প্রতি শিক্ষিত বাঙালি সমাজের দ্বিধার মূল কারণ কী?
উত্তর: বিদ্রোহের নেতৃত্বের প্রকৃতি, ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্য এবং সম্ভাব্য অরাজকতার আশঙ্কা শিক্ষিত বাঙালি সমাজকে দ্বিধান্বিত করেছিল।
প্রশ্ন: মহাবিদ্রোহের অভিজ্ঞতা শিক্ষিত বাঙালিদের পরবর্তী রাজনৈতিক চেতনার উপর কী প্রভাব ফেলেছিল?
উত্তর: বিদ্রোহের অভিজ্ঞতা শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটায় এবং ব্রিটিশ শাসনের প্রতি তাদের সমর্থন কমে যায়।